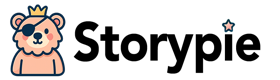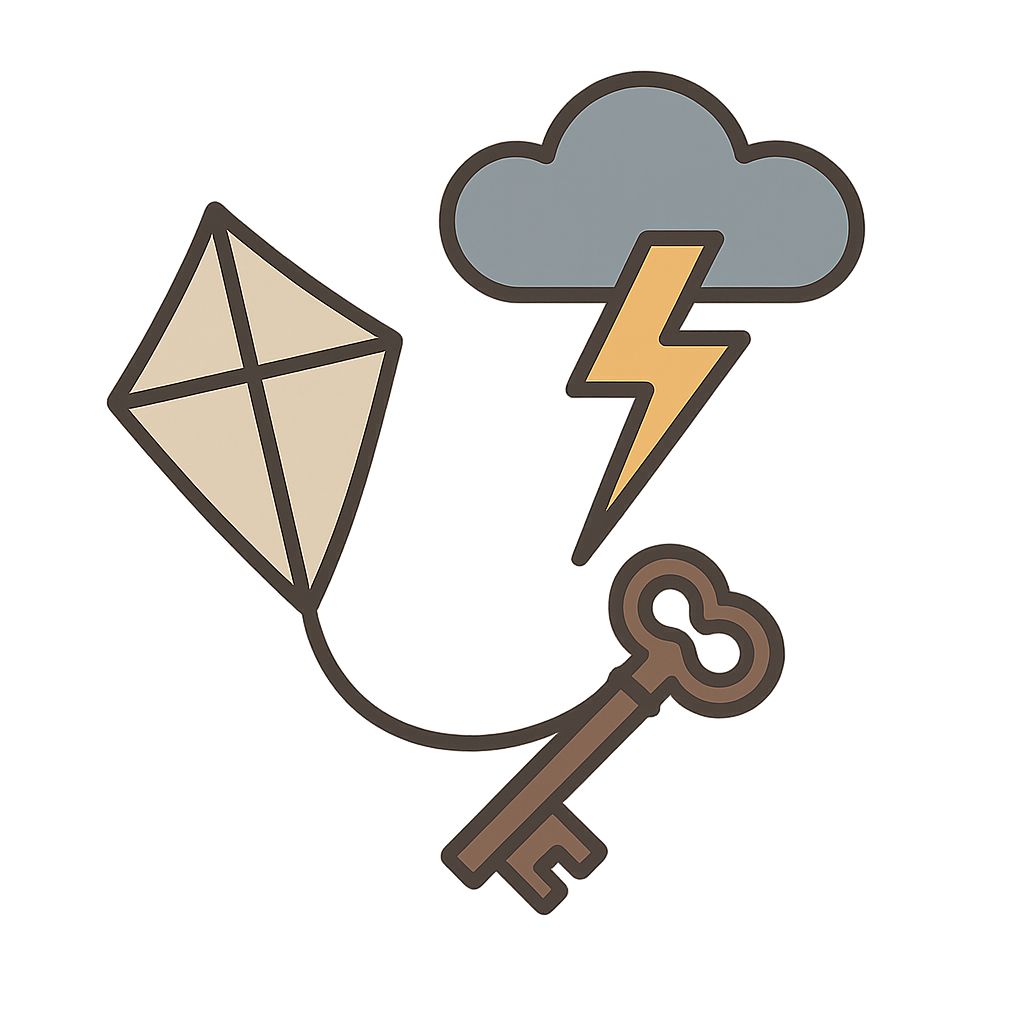বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন এবং বজ্রপাতের রহস্য
আমার নাম বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন. আমি ফিলাডেলফিয়ার একজন মুদ্রাকর, লেখক এবং উদ্ভাবক হিসেবে পরিচিত. আমি ১৭০০-এর দশকে বাস করতাম, যে সময়টা ছিল আবিষ্কার এবং অজানাকে জানার এক দারুণ যুগ. আমাদের চারপাশে জগৎটা রহস্যে ভরা ছিল, আর আমার মন সবসময় সেই রহস্য সমাধানের জন্য উন্মুখ থাকত. সেই সময়ের সবচেয়ে বড় রহস্যগুলোর মধ্যে একটি ছিল এক অদ্ভুত শক্তি, যাকে আমরা 'বৈদ্যুতিক তরল' বলতাম. আমরা জানতাম কীভাবে কাঁচের রডকে রেশম দিয়ে ঘষে ছোট ছোট স্ফুলিঙ্গ তৈরি করা যায়. পার্টিতে অতিথিদের মজা দেওয়ার জন্য আমরা এই ছোটখাটো জাদু দেখাতাম, কিন্তু কেউই সত্যিটা জানত না যে এই শক্তি আসলে কী. এটা ছিল একটা খেলার বস্তুর মতো, যার আসল ক্ষমতা আমাদের অজানা ছিল. আমি প্রায়শই আকাশ ভেঙে পড়া বিদ্যুতের দিকে তাকিয়ে থাকতাম. সেই ভয়ংকর, চোখ ধাঁধানো আলোর ঝলকানি আর মেঘের গর্জন আমাকে মুগ্ধ করত এবং ভাবাত. আমি নিজেকে প্রশ্ন করতাম, মেঘের মধ্যে থাকা এই বিশাল শক্তি আর আমাদের তৈরি করা ছোট স্ফুলিঙ্গের মধ্যে কি কোনো যোগসূত্র থাকতে পারে? আকাশের ওই ভয়ংকর বজ্রপাত কি আসলে প্রকৃতির এক বিশাল বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ? এই প্রশ্নটা আমার মাথায় ঘুরপাক খেত. বেশিরভাগ মানুষ বজ্রপাতকে ঈশ্বরের ক্রোধ বা অশুভ লক্ষণ বলে মনে করত, কিন্তু আমি বিশ্বাস করতাম এর পেছনে একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে. আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম যে এই রহস্যের সমাধান আমি করবই. আমার মনে হয়েছিল, যদি আমি প্রমাণ করতে পারি যে বজ্রপাত আর বিদ্যুৎ একই জিনিস, তাহলে আমরা হয়তো এই ধ্বংসাত্মক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার উপায় খুঁজে বের করতে পারব. এই কৌতূহলই আমাকে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় এবং বিপজ্জনক অভিযানের দিকে ঠেলে দিয়েছিল.
আমার মাথায় একটা তত্ত্ব ঘুরছিল—বজ্রপাত আসলে বিদ্যুৎ ছাড়া আর কিছুই নয়. কিন্তু একটা তত্ত্ব প্রমাণ ছাড়া মূল্যহীন. তাই আমি একটি পরীক্ষার পরিকল্পনা করলাম, যা ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং আমাকে এটি গোপনে করতে হয়েছিল. আমি যদি সবাইকে বলতাম যে আমি বজ্রপাতকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করছি, তারা হয়তো আমাকে পাগল ভাবত. আমি একটি বিশেষ ঘুড়ি তৈরি করলাম, যার কাঠামো ছিল সিডার কাঠের তৈরি এবং ডগায় একটি ধারালো ধাতব শলাকা লাগানো ছিল. ঘুড়ির সুতোটা ছিল শণের, যা ভিজে গেলে বিদ্যুৎ পরিবহন করতে পারে. সুতোর একেবারে শেষে, আমার হাতের কাছে, আমি একটি রেশমের ফিতে বেঁধেছিলাম. রেশম বিদ্যুৎ অপরিবাহী, তাই এটি আমাকে নিরাপদে রাখতে সাহায্য করবে. শণের সুতো আর রেশমের ফিতের সংযোগস্থলে আমি একটা পিতলের চাবি ঝুলিয়ে দিয়েছিলাম. আমার পরিকল্পনা ছিল, বজ্রপাতযুক্ত মেঘের কাছাকাছি ঘুড়ি ওড়ানো. যদি আমার তত্ত্ব সঠিক হয়, তাহলে মেঘের বিদ্যুৎ ধাতব শলাকা দিয়ে আকৃষ্ট হয়ে ভেজা সুতো বেয়ে নিচে নেমে আসবে এবং চাবিতে জমা হবে. অবশেষে, ১৭৫২ সালের এক ঝোড়ো জুন মাসে, সেই সুযোগ এল. আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেল, বাতাস বইতে শুরু করল আর বৃষ্টি নামল. আমার ছেলে উইলিয়ামকে সঙ্গে নিয়ে আমি শহরের বাইরে একটা ফাঁকা মাঠে গেলাম. আমরা একটা চালাঘরের নিচে আশ্রয় নিলাম যাতে আমরা শুকনো থাকতে পারি. উইলিয়ামই ছিল আমার একমাত্র সহকারী এবং সাক্ষী. উত্তেজনা আর ভয়ে আমার বুক ধড়ফড় করছিল. আমরা সাবধানে ঘুড়িটা ওড়ালাম. ঘুড়িটা মেঘের কাছাকাছি পৌঁছানোর পর আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলাম. প্রথমে কিছুই হলো না. আমি প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছিলাম. কিন্তু তারপর আমি লক্ষ্য করলাম যে শণের সুতোর আলগা আঁশগুলো খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে. এটা একটা ভালো লক্ষণ. এর মানে হল সুতোয় বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে. আমি গভীর একটা শ্বাস নিলাম. তারপর খুব সাবধানে আমার আঙুলের গাঁটটা পিতলের চাবির কাছাকাছি নিয়ে গেলাম. সঙ্গে সঙ্গে একটা নীলচে স্ফুলিঙ্গ চাবি থেকে আমার আঙুলে লাফিয়ে উঠল. আমি একটা মৃদু কিন্তু স্পষ্ট ঝটকা অনুভব করলাম. এটা ছিল এক অবিশ্বাস্য মুহূর্ত. আমি সফল হয়েছিলাম. আমি প্রমাণ করেছিলাম যে বজ্রপাত আর বিদ্যুৎ একই জিনিস. সেই ছোট স্ফুলিঙ্গটা ছিল প্রকৃতির এক বিশাল রহস্যের সমাধান. সেই রোমাঞ্চকর ঝটকা আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের মুহূর্তগুলোর মধ্যে একটি ছিল.
সেই ছোট্ট স্ফুলিঙ্গটির তাৎপর্য ছিল বিশাল. এটি প্রমাণ করেছিল যে প্রকৃতির সবচেয়ে ভয়ংকর শক্তিগুলোর একটিও কোনো দৈব ক্রোধ বা বিশৃঙ্খল ঘটনা নয়, বরং এটি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে. আর যে জিনিস নিয়ম মেনে চলে, তাকে বোঝা যায় এবং নিয়ন্ত্রণও করা যায়. এই আবিষ্কার আমার মনে এক নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিল. যদি আমরা বজ্রপাতের প্রকৃতি বুঝতে পারি, তাহলে আমরা এর থেকে নিজেদের রক্ষা করার উপায়ও খুঁজে বের করতে পারব. এই ভাবনা থেকেই আমার সবচেয়ে কার্যকরী আবিষ্কারগুলোর একটির জন্ম হয়—বজ্রনিরোধক দণ্ড বা লাইটনিং রড. আমি একটি সহজ ধারণা নিয়ে কাজ শুরু করি. বাড়ির সবচেয়ে উঁচু জায়গায় একটি ধাতব দণ্ড স্থাপন করা হবে, যা একটি তারের মাধ্যমে মাটির গভীরে সংযুক্ত থাকবে. যখন বজ্রপাত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে, তখন মেঘের বিদ্যুৎ উঁচু দণ্ডটির প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং কোনো ক্ষতি না করে তারের মাধ্যমে সোজা মাটিতে চলে যাবে. বাড়ি, গির্জা এবং জাহাজের মতো উঁচু কাঠামো, যা সবসময় বজ্রপাতের ঝুঁকিতে থাকত, সেগুলো রক্ষা করার জন্য এটি ছিল একটি যুগান্তকারী সমাধান. আমার এই আবিষ্কার দ্রুত ইউরোপ এবং আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং অগণিত জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করে. আমার এই গল্প থেকে আমি চাই তোমরা একটা জিনিস শেখো. সবকিছু শুরু হয়েছিল একটা সাধারণ প্রশ্ন দিয়ে: 'যদি এমন হয়?'. একটি সাধারণ কৌতূহল, সামান্য সাহস আর একটি অনুসন্ধিৎসু মন পৃথিবীকে বদলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে. তাই কখনো বড় প্রশ্ন করতে ভয় পেয়ো না. চারপাশের জগৎটাকে খুঁটিয়ে দেখো আর সবসময় জিজ্ঞাসা করো, 'কেন?' এবং 'কীভাবে?'. কারণ সবচেয়ে বড় আবিষ্কারগুলো প্রায়শই সবচেয়ে সহজ প্রশ্ন দিয়েই শুরু হয়.
পাঠ বোঝার প্রশ্ন
উত্তর দেখতে ক্লিক করুন